অনেকান্তবাদ
| জৈনধর্ম |
|---|
 |
|
|
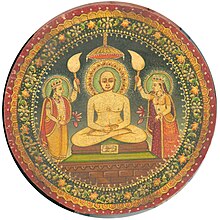
অনেকান্তবাদ (সংস্কৃত: अनेकान्तवादः, anekāntavādaḥ, "বহুতরফা") হল অধিবিদ্যামূলক সত্য-সংক্রান্ত জৈন মতবাদ। প্রাচীন ভারতে এই মতবাদটির উৎপত্তি ঘটেছিল।[১] এই মতে, পরম সত্য ও তত্ত্ব জটিল এবং বহুবিধ দিক-সমন্বিত।[২] অনেকান্তবাদকে ব্যাখ্যা করা হয় সার্বভৌমবাদ-বিরোধিতা, "বৌদ্ধিক অহিংসা",[৩] ধর্মীয় বহুত্ববাদ[৪] অর্থে; এমনকি জঙ্গি-হানা ও গণ-সহিংসতায় প্ররোচনা দেওয়া মৌলবাদকে প্রত্যাখ্যান অর্থেও।[৫] তবে কোনও কোনও গবেষকের মতে আধুনিক সংশোধনবাদীরাই অনেকান্তবাদকে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, মুক্তমনস্কতা ও বহুত্ববাদ হিসেবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন।[৬]
জৈন বিশ্বাস অনুযায়ী, কোনও একক নির্দিষ্ট মত দ্বারা অস্তিত্বের প্রকৃতি ও পরম সত্যকে বর্ণনা করা যায় না। কেবলমাত্র অরিহন্তরাই এই জ্ঞান (কেবল জ্ঞান) উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। পরম সত্য সম্পর্কে অন্যান্য জীব ও তাঁদের মতামত অসম্পূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠতর ক্ষেত্রে আংশিক সত্য।[৭] অনেকান্তবাদ অনুযায়ী, জ্ঞান-সংক্রান্ত সকল দাবিকে নিশ্চিতীকৃত হওয়া এবং প্রত্যাখ্যাত হওয়া সহ বিভিন্ন পথের মধ্যে দিয়ে যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। অনেকান্তবাদ হল জৈনধর্মের ভিত্তিগত মতবাদ।
অনেকান্তবাদের উৎসটি পাওয়া যায় ২৪শ জৈন তীর্থংকর মহাবীরের (খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৯-৫২৭ অব্দ) শিক্ষায়।[৮] অনেকান্তবাদ থেকেই মধ্যযুগে স্যাদ্বাদ ("নিরূপিত দৃষ্টিভঙ্গি") ও নয়বাদের ("আংশিক দৃষ্টিভঙ্গি") মতো দ্বান্দ্বিকতামূলক মতবাদের উদ্ভব ঘটে, যা জৈনধর্মের অধিকতর বিস্তারিত যৌক্তিক রূপ ও অভিব্যক্তি দান করে। খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দে জৈন, বৌদ্ধ ও বৈদিক দার্শনিক ধারার পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের মধ্য দিয়ে জৈনধর্মে এই মতবাদটির বিস্তারিত রূপটির উদ্ভব ঘটে।[৯]
নাম-ব্যুৎপত্তি
[সম্পাদনা]"অনেকান্তবাদ" শব্দটি "অনেকান্ত" ও "বাদ" এই দু’টি সংস্কৃত শব্দ নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে "অনেকান্ত" শব্দটিই তিনটি মূল শব্দ নিয়ে গঠিত। যথা: "অন" (না), "এক" ও "অন্ত" (শেষ, দিক)। সন্ধিবদ্ধ হয়ে এই শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় "[যা] এক-প্রান্তিক বা একতরফা নয়", "যা বহু-তরফা" বা "বহুমুখীত্ব"।[১০][১১][১২] "বাদ" শব্দটির অর্থ "মতবাদ, পন্থা, কথন, তত্ত্ব"।[১৩][১৪] বিষেষজ্ঞেরা "অনেকান্তবাদ" কথাটির অনুবাদ করেন "বহুতরফা",[১৫][১৬] "অ-একতরফা"[১৭] বা "বহুমুখিতা"র[১৮] মতবাদ হিসেবে।
জৈনধর্মের শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের আদি আনুশাসনিক ধর্মগ্রন্থগুলিতে "অনেকান্তবাদ" কথাটি পাওয়া যায় না। যদিও এই সব শ্বেতাম্বর ধর্মগ্রন্থে উদ্ধৃত মহাবীর কথিত ব্যক্তির দৃষ্টিকোণের উপর সান্ত ও অনন্তের নির্ভরশীলতা-সংক্রান্ত মন্তব্যগুলির মধ্যে এই মতবাদের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। সত্যকে অনন্ত ভাবে প্রকাশ করা যায় বলে মহাবীর যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাকে "অনেকান্তবাদ" নামে প্রথম অভিহিত করেন আচার্য সিদ্ধসেন দিবাকর। আচার্য উমাস্বামী রচিত তত্ত্বার্থসূত্র গ্রন্থে প্রথম অনেকান্তবাদ মতবাদের আদিতম সার্বিক শিক্ষাগুলি পাওয়া যায়। সকল জৈন সম্প্রদায়ের কাছেই এই গ্রন্থটি প্রামাণ্য। দিগম্বর জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে কুন্দকুন্দের দ্বি-সত্য তত্ত্ব এই মতবাদের মূল ভিত্তিটি গঠন করেছে।[১৮]
দার্শনিক মতবাদ
[সম্পাদনা]প্রকৃত প্রস্তাবে জৈন অনেকান্তবাদ মতটি উৎসারিত হয়েছিল সত্যের ভিন্ন ভিন্ন সকল দার্শনিক ব্যাখ্যা ও তত্ত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সেগুলির মধ্যে সাম্যবিধান করার একটি সামাজিক প্রয়াস হিসেবে। সত্য এক ও পরম হতে পারে না, বরং তার বহু-দিকসমন্বিত রূপ থাকা সম্ভব এবং সেই কারণে কোনও এক ব্যক্তির কাছে যা সত্য তা অন্যের কাছে সত্য নাও হতে পারে—এই মতবাদের ফলে জৈনধর্মে সত্য সম্পর্কে ধারণাটি সমৃদ্ধি লাভ করে। অনেকান্তবাদ সত্য সম্পর্কে একটি সমন্বয়মূলক সুখকর ধারণা প্রস্তাব করে। এই মতে, বিভিন্ন জনে সত্যের বিভিন্ন রূপ দর্শন করেন এবং সকলের উচিত সত্য সম্পর্কে অপরের ধারণাকে সম্মান করা। এইভাবেই সমাজের অগ্রগতি সম্ভব এবং এই উপায়েই সকল সংঘাত মিটিয়ে সমাজে শান্তি আনয়ন করা যায়। অনেকান্তবাদ বা অনেকান্তত্ব দর্শনে বলা হয়েছে, সত্য জটিল এবং সব ক্ষেত্রেই তা বহু-অবয়ববিশিষ্ট। সত্য অনুভব করা যায়, কিন্তু তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্পূর্ণত সম্ভব নয়। মানুষের প্রকাশের প্রয়াসটি হল মায়া বা "সত্যের আংশিক অভিপ্রকাশ"।[১০][১১] ভাষা সত্য নয়, কিন্তু তা সত্য প্রকাশের একটি উপায় ও প্রয়াস। মহাবীরের মতে, সত্য থেকে ভাষা ফিরে আসে, অন্যান্য পন্থাগুলি ফিরতে পারে না।[১০][১৯] ব্যক্তিবিশেষ এক প্রকার সত্য অনুভব করতে পারে, কিন্তু সেই অনুভূতিটি ভাষার মাধ্যমে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারে না। অনুভূতিটি প্রকাশ করার সকল প্রয়াসই জৈন মতে স্যাৎ বা "একদিক থেকে" সিদ্ধ, কিন্তু তাও সেক্ষেত্রে "সম্ভবত, শুধুমাত্র একটি দৃষ্টিভঙ্গি ও অসম্পূর্ণ" কথাগুলি থেকেই যায়।[১৯] একইভাবে আধ্যাত্মিক সত্যগুলিও জটিল, বহু-দিকবিশিষ্ট এবং সেগুলির বহুত্বও ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; কিন্তু চেষ্টা ও যথাযথ কর্মের মাধ্যমে তা অনুভব করা সম্ভব।[১০]
জৈনদের অনেকান্তবাদ ধারণাটি যে প্রাচীন তার প্রমাণ সামান্নফল সুত্তের ন্যায় বৌদ্ধ গ্রন্থে এই মতবাদের উল্লেখ। জৈন আগম শাস্ত্র থেকে জানা যায়, মহাবীর সকল অধিবিদ্যামূলক দার্শনিক প্রশ্নের উত্তরে একটি "সীমায়িত হ্যাঁ" (স্যাৎ) ব্যবহার করতেন।[২০][২১] এই গ্রন্থগুলিতে অনেকান্তবাদ দর্শনকে মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের উপদেশাবলির অন্যতম প্রধান পার্থক্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অধিবিদ্যামূলক প্রশ্নের উত্তরে "হ্যাঁ" অথবা "না"-জাতীয় চূড়ান্ত মত প্রত্যাখ্যান করে বুদ্ধ মধ্যপন্থা শিক্ষা দিয়েছিলেন। অপরপক্ষে মহাবীর তাঁর অনুগামীদের "সম্ভবত"-র শর্তসাপেক্ষে "হ্যাঁ" ও "না" দুই উত্তরকে গ্রহণ করার এবং পরম সত্যকে সামঞ্জস্যবিধানের মাধ্যমে অনুভব করার শিক্ষা দিয়েছিলেন।[২২] জৈনধর্মের স্যাদ্বাদ (ভাবীকথনমূলক যুক্তিবিদ্যা) ও নয়বাদ (দৃষ্টিভঙ্গিগত জ্ঞানতত্ত্ব) অনেকান্তবাদ ধারণার উপর প্রসার লাভ করেছে। স্যাদ্বাদ অস্তিত্বের প্রকৃতি বর্ণনাকারী প্রতিটি শব্দবন্ধ বা অভিব্যক্তির সঙ্গে অনুসর্গ হিসেবে "স্যাদ্" শব্দটির প্রয়োগের মাধ্যমে অনেকান্ত অভিব্যক্তির প্রকাশের পক্ষপাতী।[২৩][২৪]
বিমল মতিলাল লিখেছেন, জৈন অনেকান্তবাদ মনে করে "কোনও দার্শনিক বা অধিবিদ্যামূলক বিবৃতিই সত্য হতে পারে না যদি না তার সঙ্গে কোনও শর্ত বা সীমাবদ্ধতা আরোপিত না হয়"।[২৫] জৈন মতে, যে অধিবিদ্যামূলক বিবৃতির সঙ্গে এক বা একাধিক শর্ত (স্যাদ্বাদ) বা সীমাবদ্ধতা (নয়বাদ, অর্থাৎ দৃষ্টিকোণ) যুক্ত হলে তবেই তা সত্য হয়।[২৬]
তথ্যসূত্র
[সম্পাদনা]উল্লেখপঞ্জি
[সম্পাদনা]- ↑ কর্ট ২০০০, পৃ. ৩২৫-৩২৬, ৩৪২।
- ↑ ডুন্ডাস, পল (২০০৪)। "বিয়ন্ড অনেকান্তবাদ: আ জৈন আপ্রোচ টু রিলিজিয়াস টলারেন্স"। তারা শেঠিয়া। অহিংসা, অনেকান্ত, অ্যান্ড জৈনিজম। দিল্লি: মোতিলাল বনারসিদাস পাবলিশার্র। পৃষ্ঠা ১২৩–১৩৬। আইএসবিএন 81-208-2036-3।
- ↑ কর্ট ২০০০, পৃ. ৩২৪।
- ↑ উইলি ২০০৯, পৃ. ৩৬।
- ↑ কোলার, জন (২০০৪)। "হোয়াই ইজ অনেকান্তবাদ ইমপর্টেন্ট?"। তারা শেঠিয়া। অহিংসা, অনেকান্ত, ও জৈনধর্ম। দিল্লি: মোতিলাল বনারসিদাস। পৃষ্ঠা ৮৫–৪৪। আইএসবিএন 81-208-2036-3।
- ↑ কর্ট ২০০০, পৃ. ৩২৯-৩৩৪।
- ↑ জৈনি ১৯৯৮, পৃ. ৯১।
- ↑ মতিলাল ১৯৮১, পৃ. ২-৩।
- ↑ মতিলাল ১৯৮১, পৃ. ১-২।
- ↑ ক খ গ ঘ চরিত্রপ্রজ্ঞা ২০০৪, পৃ. ৭৫–৭৯।
- ↑ ক খ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ২২৯–২৩১।
- ↑ গ্রিমস, জন (১৯৯৬) পৃ. ৩৪
- ↑ মনিয়ার মনিয়ার-উইলিয়ামস (১৮৯৯), "वाद", সংস্কৃত ইংলিশ ডিকশনারি উইথ এটিমোলজি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃ. ৯৩৯-৯৪০
- ↑ ফিলিপ সি. অ্যালমন্ড (১৯৮২)। মিস্টিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড রিলিজিয়াস ডকট্রেইন: অ্যান ইনভেস্টিগেশন অফ দ্য স্টাডি অফ মিস্টিসিজম ইন ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নস। ওয়াল্টার ডে গ্রুয়েটার। পৃষ্ঠা ৭৫। আইএসবিএন 978-90-279-3160-3।
- ↑ নিকোলাস এফ. গিয়ার (২০০০)। স্পিরিচুয়াল টাইটানিজম: ইন্ডিয়ান, চাইনিজ, অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন পার্সপেক্টিভ। স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক প্রেস। পৃষ্ঠা ৮০, ৯০–৯২। আইএসবিএন 978-0-7914-4528-0।
- ↑ অ্যান্ড্রু আর. মার্ফি (২০১১)। দ্য ব্ল্যাকওয়েল কমপ্যানিয়ন টু রিলিজিয়ন অ্যান্ড ভায়োলেন্স। জন উইলি অ্যান্ড সন্স। পৃষ্ঠা ২৬৭–২৬৯। আইএসবিএন 978-1-4051-9131-9।
- ↑ মতিলাল ১৯৮১, পৃ. ১।
- ↑ ক খ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ২২৯-২৩১।
- ↑ ক খ জৈন দর্শন, আইইপি, মার্ক ওয়েন ওয়েব, টেক্সাস টেক ইউনিভার্সিটি
- ↑ মতিলাল ১৯৯০, পৃ. ৩০১–৩০৫।
- ↑ বালসারোউইকজ ২০১৫, পৃ. ২০৫–২১৮।
- ↑ মতিলাল ১৯৯৮, পৃ. ১২৮–১৩৫।
- ↑ কোলার ২০০০, পৃ. ৪০০–৪০৭।
- ↑ স্যানগেভ ২০০৬, পৃ. ৪৮-৫১।
- ↑ {{উদ্ধৃতি: "...no philosophic or metaphysical proposition can be true if it is asserted without any condition or limitation".
- ↑ মতিলাল ১৯৮১, পৃ. ২-৩, ৩০-৩২, ৫২-৫৪।
গ্রন্থপঞ্জি
[সম্পাদনা]- বালসারোউইকজ, পায়োটর্ (২০১৫), আর্লি অ্যাসেটিকিজম ইন ইন্ডিয়া: আজীবিকিজম অ্যান্ড জৈনিজম, রটলেজ, আইএসবিএন 978-1-317-53853-0
- আচার্য সিদ্ধসেন দিবাকর (২০০৪)। ভদ্রংকর বিজয় গানি, সম্পাদক। বর্ধমান দ্বত্রিংশিকা। জয়পুর: প্রাকৃত ভারতী অ্যাকাডেমি।
- ধ্রুব, এ. বি., সম্পাদক (১৯৩৩)। স্যাদবাদমঞ্জরী অফ মল্লিসেন উইথ দি অন্য-যোগ-ব্যবচ্ছেদ-দ্বত্রিংশিকা অফ হেমচন্দ্র। বোম্বাই: সংস্কৃত অ্যান্ড প্রাকৃত সিরিজ নং ৮৩।
- বার্চ, জর্জ বসওয়ার্থ (১৯৬৪)। "সেভেন-ভ্যালুড লজিক ইন জৈন ফিলোজফি"। ইন্টারন্যাশানাল ফিলোজফিক্যাল কোয়ার্টারলি। ব্রংক্স, নিউ ইয়র্ক। ৪ (১): ৬৮–৯৩। আইএসএসএন 0019-0365। ডিওআই:10.5840/ipq19644140। ১০ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা।
- চট্টোপাধ্যায়, তারা (২০০১)। নলেজ অ্যান্ড ফ্রিডম ইন ইন্ডিয়ান ফিলোজফি। ল্যানহ্যাম, মেরিল্যান্ড: লেক্সিংটন বুকস। আইএসবিএন 0-7391-0692-9।
- কর্ট, জন (২০০০)। "ইন্টেলেকচুয়াল অহিংসা রিভিজিটেড: জৈন টলারেন্স অ্যান্ড ইনটলারেন্স অফ আদার্স"। ফিলোজফি ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট। ইউনিভার্সিটি অফ হাওয়াই প্রেস। ৫০ (৩): ৩২৪–৪৭। জেস্টোর 1400177।
- দাশগুপ্ত, এস. এন. (১৯৩২)। হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান ফিলোজফি। দ্বিতীয় খণ্ড। কেমব্রিজ: কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।
- দুলি চন্দ্র জৈন, সম্পাদক (১৯৯৭)। স্টাডিজ ইন জৈনিজম: রিডার ২। নিউ ইয়র্ক: জৈন স্টাডি সার্কেল আইএনসি.। আইএসবিএন 0-9626105-2-6।
- ডুন্ডাস, পল (২০০২) [১৯৯২], দ্য জৈনস (দ্বিতীয় সংস্করণ), লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক: রটলেজ, আইএসবিএন 0-415-26605-X
- ডুন্ডাস, পল (২০০৬), অলিভেল, প্যাট্রিক, সম্পাদক, বিটুইন দি এম্পায়ারস: সোসাইটি ইন ইন্ডিয়া ৩০০ বিসিই টু ৪০০ সিই, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, আইএসবিএন 978-0-19-977507-1
- নগেন্দ্র কুমার সিং, সম্পাদক (২০০১)। এনসাইক্লোপিডিয়া অফ জৈনিজম। নতুন দিল্লি: আনমোল পাবলিকেশনস। আইএসবিএন 81-261-0691-3।
- জৈন, জে. সি. (২০০১)। "ডেভেলপমেন্ট অফ ডকট্রেইন অফ অনেকান্তবাদ"। নগেন্দ্র কুমার সিং। এনসাইক্লোপিডিয়া অফ জৈনিজম। নতুন দিল্লি: আনমোল পাবলিকেশনস। আইএসবিএন 81-261-0691-3।
- পাণ্ড্য, ভি. (২০০১), "রিফিউটেশন অফ জৈন দর্শন বাই শংকরাচার্য", নগেন্দ্র কুমার সিং, এনসাইক্লোপিডিয়া অফ জৈনিজম, নতুন দিল্লি: আনমোল পাবলিকেশনস, আইএসবিএন 81-261-0691-3
- উপাধ্যায়, এ. এন. (২০০১)। "স্যাদবাদ ইন দি অর্ধমাগধী ক্যানন"। নগেন্দ্র কুমার সিং। এনসাইক্লোপিডিয়া অফ জৈনিজম। নতুন দিল্লি: আনমোল পাবলিকেশনস। আইএসবিএন 81-261-0691-3।
- গান্ধী, মোহনদাস (১৯৯৫)। জিতেন্দ্র ঠাকোরভাই দেসাই, (সংকলন) আর. কে. প্রভু, সম্পাদক। ট্রুথ ইজ গড: গ্লিনিংস ফ্রম দ্য রাইটিংস অফ মহাত্মা গান্ধী বিয়ারিং অন গড, গড-রিয়ালাইজেশন অ্যান্ড গডলি ওয়ে। আমেদাবাদ: নবজীবন পাবলিশিং হাউস।
- গ্রিমস, জন (১৯৯৬)। আ কনসাইস ডিকশনারি অফ ইন্ডিয়ান ফিলোজফি: সংস্কৃত টার্মস ডেফাইন্ড ইন ইংলিশ। নিউ ইয়র্ক: সানি প্রেস। আইএসবিএন 0-7914-3068-5।
- হামফ্রেজ, ক্রিসমাস (১৯৬৯)। দ্য বুদ্ধিস্ট ওয়ে অফ লাইফ। লন্ডন: আনউইন বুকস।
- হিরিআন্না, এম. (১৯৯৩), আউটলাইনস অফ ইন্ডিয়ান ফিলোজফি, মোতিলাল বনারসিদাস, আইএসবিএন 978-81-208-1086-0
- জৈনি, পদ্মনাভ এস. (১৯৯৮) [১৯৭৯], দ্য জৈন পাথ অফ পিউরিফিকেশন, দিল্লি: মোতিলাল বনারসিদাস, আইএসবিএন 81-208-1578-5
- জোনস, জেমস উইলিয়াম (২০০৮), ব্লাড দ্যাট ক্রাইস আউট ফ্রম দি আর্থ: দ্য সাইকোলজি অফ রিলিজিয়াস টেরোরিজম, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, আইএসবিএন 978-0-19-804431-4
- জেকবি, হারম্যান (১৮৮৪)। এফ. ম্যাক্স মুলার, সম্পাদক। দি আচারাঙ্গ সূত্র। সেক্রেড বুকস অফ দি ইস্ট, দ্বাবিংশ খণ্ড, প্রথম ভাগ (ইংরেজি ভাষায়)। অক্সফোর্ড: দ্য ক্ল্যারেনডন প্রেস। আইএসবিএন 0-7007-1538-X। দ্রষ্টব্য: উল্লিখিত আইএসবিএন-টি যুক্তরাষ্ট্রের রটলেজ (২০০১) পুনর্মুদ্রণের। কিন্তু ইউআরএলটি মূল ১৮৮৪ মুদ্রণের স্ক্যান সংস্করণ।
- জেকবি, হারম্যান (১৮৯৫)। এফ. ম্যাক্স মুলার, সম্পাদক। দ্য সূত্রকৃতঙ্গ (ইংরেজি ভাষায়)। অক্সফোর্ড: দ্য ক্ল্যারেনডন প্রেস। আইএসবিএন 0-7007-1538-X। দ্রষ্টব্য: উল্লিখিত আইএসবিএন-টি যুক্তরাষ্ট্রের রটলেজ (২০০১) পুনর্মুদ্রণের। কিন্তু ইউআরএলটি মূল ১৮৯৫ মুদ্রণের স্ক্যান সংস্করণ।
- জৈন, বিজয় কে (১ জানুয়ারি ২০১৬), আচার্য সামন্তভদ্র’স আপ্তমীমাংসা (দেবাগমস্তোত্র), আইএসবিএন 9788190363983
- জৈন, জে. পি. (২০০৬)। দি আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স অফ সেলফ রিয়্যালাইজেশন: পুরুষার্থসিদ্ধিউপায় অফ আচার্য অমৃতচন্দ্র (সংস্কৃত and ইংরেজি ভাষায়)। দিল্লি: রেডিয়েন্ট পাবলিশার্স।
- কোলার, জন এম. (২০০০)। "স্যাদবাদ অ্যাজ দি এপিস্টেমোলজিক্যাল কি টু দ্য জৈন মিডল ওয়ে মেটাফিজিক্স অফ অনেকান্তবাদ"। ফিলোজফি ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট। হোনোলুলু। ৫০ (৩): ৬২৮–৬৩০। আইএসএসএন 0031-8221। এসটুসিআইডি 170240551। জেস্টোর 1400182। ডিওআই:10.1353/pew.2000.0009।
- লং, জেফরি ডি. (২০০৯), জৈনিজম: অ্যান ইন্ট্রোডাকশন, আই. বি. টরিস, আইএসবিএন 978-0-8577-3656-7
- লং, জেফরি ডি. (২০১৩), জৈনিজম: অ্যান ইন্ট্রোডাকশন, আই. বি. টরিস, আইএসবিএন 978-0-8577-1392-6
- মতিলাল, বিমল কৃষ্ণ (১৯৯০), লজিক, ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড রিয়্যালিটি: ইন্ডিয়ান ফিলোজফি অ্যান্ড কন্টেম্পোরারি ইস্যুজ, মোতিলাল বনারসিদাস, আইএসবিএন 978-81-208-0717-4
- মতিলাল, বিমল কৃষ্ণ (১৯৯৮), গানেরি, জনার্দন; তিওয়ারি, হিরামন, সম্পাদকগণ, দ্য ক্যারেক্টার অফ লজিক ইন ইন্ডিয়া, স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক প্রেস, আইএসবিএন 978-0-7914-3739-1
- মজুমদার, উমা (২০০৫)। গান্ধী’জ পিলগ্রিমেজ অফ ফেইথ: ফ্রম ডার্কনেস টু লাইট। নিউ ইয়র্ক: সানি প্রেস। আইএসবিএন 0-7914-6405-9।
- মতিলাল, বি. কে. (১৯৮১), দ্য সেন্ট্রাল ফিলোজফি অফ জৈনিজম (অনেকান্তবাদ), এল. ডি. সিরিজ ৭৯, আমেদাবাদ
- ম্যাকইভিলে, টমাস (২০০২)। দ্য শেপ অফ এনশিয়েন্ট থট: কমপ্যারাটিভ স্টাডিজ ইন গ্রিক অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ফিলোজফিজ। নিউ ইয়র্ক: অলওয়ার্থ কমিউনিকেশনস, আইএনসি। আইএসবিএন 1-58115-203-5।
- নাকামুরা, হাজিম (১৯৯২)। কমপ্যারাটিভ হিস্ট্রি অফ আইডিয়াজ। দিল্লি: মোতিলাল বনারসিদাস। আইএসবিএন 81-208-1004-X।
- সেঠিয়া, তারা (২০০৪), অহিংসা, অনেকান্ত অ্যান্ড জৈনিজম, মোতিলাল বনারসিদাস, আইএসবিএন 978-81-208-2036-4
- চরিত্রপ্রজ্ঞা, সামানি (২০০৪)। "মহাবীর, অনেকান্তবাদ অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড টুডে"। তারা শেঠিয়া। অহিংসা, অনেকান্ত অ্যান্ড জৈনিজম। দিল্লি: মোতিলাল বনারসিদাস। পৃষ্ঠা ৭৫–৮৯। আইএসবিএন 81-208-2036-3।
- জৈন, কমলা (২০০৪)। "অনেকান্তবাদ ইন প্রেজেন্ট ডে সোশ্যাল লাইফ"। তারা শেঠিয়া। অহিংসা, অনেকান্ত অ্যান্ড জৈনিজম। দিল্লি: মোতিলাল বনারসিদাস। পৃষ্ঠা 113–122। আইএসবিএন 81-208-2036-3।
- ভ্যালেলি, অ্যানি (২০০৪)। "অনেকান্ত, অহিংসা অ্যান্ড কোয়েশ্চেন অফ প্লুর্যালিজম"। তারা শেঠিয়া। অহিংসা, অনেকান্ত অ্যান্ড জৈনিজম। দিল্লি: মোতলাল বনারসিদাস। পৃষ্ঠা ৯৯–১১২। আইএসবিএন 81-208-2036-3।
- সাঙ্গাভে, বিলাস আদিনাথ (২০০৬) [১৯৯০], অ্যাসপেক্টস অফ জৈন রিলিজিয়ন (৫ সংস্করণ), ভারতীয় জ্ঞানপীঠ, আইএসবিএন 81-263-1273-4
- শোয়ার্ৎজ, ডব্লিউএম. অ্যান্ড্রু (২০১৮), দ্য মেটাফিজিক্স অফ প্যারাডক্স: জৈনিজম, অ্যাবসোলিউট রিলেটিভিটি, অ্যান্ড রিলিজিয়াস প্লুর্যালিজম, লেক্সিংটন বুকস, আইএসবিএন 9781498563925
- শাহ, নাটুভাই (১৯৯৮)। জৈনিজম: দ্য ওয়ার্ল্ড অফ কঙ্কারারস। খণ্ড ১ ও ২। সাসেক্স: সাসেক্স অ্যাকাডেমি প্রেস। আইএসবিএন 1-898723-30-3।
- শর্মা, অরবিন্দ (২০০১)। জৈন পার্সপেক্টিভ অন দ্য ফিলোজফি অফ রিলিজিয়ন। দিল্লি: মোতিলাল বনারসিদাস। আইএসবিএন 81-208-1760-5।
- সোনলিটনার, মাইকেল ডব্লিউ (১৯৮৫)। গান্ধিয়ান ননভায়োলেন্স: লেভেলস অফ সত্যাগ্রহ। ভারত: অভিনব পাবলিকেশনস। আইএসবিএন 81-7017-205-5।
- টি. ডব্লিউ. রাইস ডেভিডস (১৯৮০)। সেক্রেড বুকস অফ দি ইস্ট। দিল্লি: মোতিলাল বনারসিদাস। আইএসবিএন 81-208-0101-6।
- ওয়েব, মার্ক ওয়েন। "দ্য জৈন ফিলোজফি"। দি ইন্টারনেট এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ফিলোজফি। ২ মার্চ ২০০৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০০৮-০৩-১৮।
- উইলি, ক্রিস্টি এল. (২০০৯), দি এ টু জেড অফ জৈনিজম, ৩৮, স্কেয়ারক্রো, আইএসবিএন 978-0-8108-6337-8
- উইলি, ক্রিস্টি এল. (২০০৪)। হিস্টোরিক্যাল ডিকশনারি অফ জৈনিজম। স্কেয়ারক্রো। আইএসবিএন 978-0-8108-6558-7।
বহিঃসংযোগ
[সম্পাদনা]- দ্য ডকট্রেইন অফ রিলেটিভ প্লুর্যালিজম (অনেকান্তবাদ), সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ১৯৪০
- অনেকান্তবাদ প্রসঙ্গে প্রবীণ কে. শাহ
- দি ইন্ডিয়ান-জৈন ডায়ালেকটিক অফ স্যাদবাদ ইন রিলেশন টু প্রব্যাবিলিটি, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, ডায়ালেক্টিকা ৮, ১৯৫৪, ৯৫–১১১।
- দ্য স্যাদবাদ সিস্টেম অফ প্রেডিকেশন, জে. বি. এস. হ্যালডেন, সাংখ্য ১৮, ১৯৫–২০০, ১৯৫৭।
- অনেকান্তবাদ ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ১৭ মে ২০১৩ তারিখে
- দ্য প্লুর্যালিজম প্রোজেক্ট - হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়