বাংলাদেশের স্থাপত্য
| বাংলাদেশের সংস্কৃতি |
|---|
| বিষয় সম্পর্কিত ধারাবাহিক |
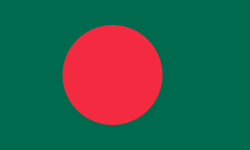 |
বাংলাদেশের স্থাপত্য বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থাপনার গঠন বৈশিষ্ট্য ও শৈলীকে বোঝায়।[১] বাংলাদেশের স্থাপত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে যার মূল রয়েছে এদেশের সংস্কৃতি, ধর্ম এবং ইতিহাসের মাঝে।[২] এটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিকশিত এবং সামাজিক, ধর্মীয়, বহুজাতিক সম্প্রদায়ের প্রভাবে তৈরি। বাংলাদেশের স্থাপত্য এদেশের মানুষের জীবনধারা, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক স্থাপত্যের পাশাপাশি বাংলাদেশে অসংখ্য স্থাপত্য নিদর্শন ও ধ্বংসাবশেষ রয়েছে যেগুলো হাজার বছরের পুরনো।
পাল বৌদ্ধ স্থাপত্য
[সম্পাদনা]বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশ ও যার অন্তর্ভুক্ত ছিল) ভারতীয় বৌদ্ধ শাসনের প্রথম দিককার সাম্রাজ্য ছিল পাল সাম্রাজ্য যারা অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত শাসন করে। পাল গণ স্থাপত্যের একটি নতুন ধারা তৈরি করে যা পাল ভাস্কর্য শিল্প বিদ্যালয় নামে পরিচিত ছিল। সুবিশাল বিক্রমশিলা বিহার, ওদন্তপুরু বিহার এবং জগদ্দল বিহার ছিল পালদের কিছু উল্লেখযোগ্য কীর্তি। ধর্মপাল কর্তৃক পাহাড়পুরে স্থাপিত সোমপুর মহাবিহার উপমহাদেশের বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহার এবং একে পৃথিবীর চোখে সৌন্দর্য হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইউনেস্কো ১৯৮৫ সালে একে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, চীন, জাপান এবং তিব্বত জুড়ে পাল স্থাপত্য অনুসরণ করা হচ্ছিল। বাংলা যথার্থই "পূর্বের কর্ত্রী" উপাধি অর্জন করে। ড. স্টেল্লা ক্রাম্রিস্ক বলেন: "বিহার এবং বাংলার স্থাপত্য নেপাল, বার্মা, শ্রীলঙ্কা এবং জাভার উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে।" ধীমান এবং ভিত্তপাল ছিলেন দুইজন বিখ্যাত পাল ভাস্কর। সোমপুর মহাবিহার সম্পর্কে জনাব জে.সি. ফ্রেঞ্চ দুঃখের সাথে বলেন: "মিশরের পিরামিডের উপর গবেষণার জন্য আমরা প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করি। কিন্তু আমরা যদি ঐ অর্থের শতকরা মাত্র এক ভাগ সোমপুর মহাবিহারের খননে খরচ করতাম, কে জানে কিরকম আশ্চর্যজনক আবিষ্কার সম্ভব হত।"[৩]
ইসলামিক এবং মুঘল স্থাপত্য
[সম্পাদনা]বাংলার সালতানাত ছিল ১৩৪২ থেকে ১৫৭৬ এর মধ্যবর্তী সেই সময় যখন মধ্য এশীয় বংশোদ্ভূত মুসলিম নবাবেরা মুঘল সাম্রাজ্য থেকে প্রভাবমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে শাসন করছিলেন। এই সময়ের অধিকাংশ মুসলিম স্থাপত্য পাওয়া যায় গৌড় অঞ্চলে, যা আজকের রাজশাহী বিভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলা জুড়ে ছিল। এই সময়ের স্থাপত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল স্থানীয় বাঙালি স্থাপত্য ঐতিহ্যের প্রভাব। সালতানাতের স্থাপত্যের প্রভাব বিস্তার করেছিল ষাট গম্বুজ মসজিদ, সোনা মসজিদ এবং কুসুম্বা মসজিদ এর মত স্থাপত্যতে।[৪]
১৫৭৬ এর দিকে মুঘল সাম্রাজ্য বাংলার বেশিরভাগ জায়গায় বিস্তার লাভ করে। ঢাকা মুঘলদের সামরিক ঘাঁটি হিসেবে আবির্ভাব হয়। ১৬০৮ সালে সুবাদার প্রথম ইসলাম খান শহরটিকে বাংলা সুবাহর রাজধানী হিসেবে ঘোষণা দিলে নগরায়ন এবং আবাসন এর ব্যাপক উন্নতির ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং এই সময়ে অসংখ্য মসজিদ এবং দুর্গ নির্মাণ হতে থাকে। বড় কাটরা নির্মাণ করা হয়েছিল ১৬৪৪ থেকে ১৬৪৬ সালের মধ্যে, সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজার দাপ্তরিক বাসভবন হিসেবে।
আজকের বাংলাদেশে ভারতীয় মুঘল স্থাপত্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছায় সুবেদার শায়েস্তা খানের শাসনামলে, যিনি আধুনিক নগরায়ন ও সরকারি স্থাপত্যকে উৎসাহ দিয়ে একটি বিশাল মাত্রার নগরায়ন ও অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ শুরু করেন।তিনি শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং প্রদেশজুড়ে অসংখ্য বিশাল স্থাপত্য যেমন মসজিদ, সমাধিসৌধ এবং প্রাসাদ নির্মাণে উৎসাহ দিয়েছেন, যেগুলো কিছু সেরা মুঘল স্থাপত্য নিদর্শনের প্রতিনিধিত্ব করত। খান লালবাগ কেল্লা (আওরঙ্গবাদ কেল্লা নামেও পরিচিত), চক বাজার মসজিদ, সাত মসজিদ এবং ছোট কাটরার ব্যাপক সম্প্রসারণ করেন। তিনি তার কণ্যা পরীবিবির সমাধিসৌধের নির্মাণ কাজ তদারকি করেন।
-
১৯ শতকে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে সাত মসজিদ
টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য
[সম্পাদনা]বাংলাদেশের বেশিরভাগ টেরাকোটা মন্দির মুসলিম শাসনের শেষভাগে এবং ব্রিটিশ শাসনের শুরুর দিকে অর্থবান হিন্দু জমিদারদের উদ্যোগে তৈরি।
- মন্দির স্থাপত্যের ধরনঃ
- একবাংলা, একটি বাঁকা ছাঁদ, যার দুটি ঢাল।
- জোড়বাংলা, একবাংলা অথবা দো-চালা ধরনের ছাঁদ, যার দুটি বাঁকা অংশ একটি বাঁকা চূড়ায় এসে মিশে।
- এক-চালা, এক তলা, অথবা একটি ঢালু ছাঁদ বিশিষ্ট দুই তলা স্থাপত্য।
- দোচালা, একটি বাঁকা ছাঁদ, যার দুটি ঢাল।
- চারচালা, চারটি ত্রিকোণাকার খণ্ডের সমন্বয়ে তৈরি একটি বাঁকা ছাঁদ বিশিষ্ট। have a curved roof composed of four triangular segments
- আটচালা, মূল স্তম্ভ চারকোণা চারচালা মন্দিরের মত। কিন্তু শীর্ষে মূল স্তম্ভের একটি ছোট কাঠামো থাকে।
- ডেউল, সাধারণত ছোট আকারের এবং ইসলামিক স্থাপত্যের কিছু বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত।
- একরত্ন, মূল স্তম্ভ চারকোণা চারচালা মন্দিরের মত। কিন্তু ছাঁদ অন্যরকম, সমতল এবং কেন্দ্রে একটি টাওয়ার বিশিষ্ট।
- পঞ্চরত্ন, ছাঁদে পাঁচটি টাওয়ার আছে; চারটি মূল স্তরের কোণায় থাকে, একটি মাঝে থাকে।
- নবরত্ন, দুইটি মূল স্তর নিয়ে গঠিত, যার প্রতিটিতে চারটি করে সুউচ্চ চূড়া, একেকটি একেক কোনায় এবং মাঝখানে একটি চূড়া। মোট নয়টি।
-
বাইরে টেরাকোটা নকশা বিশিষ্ট কান্তজির মন্দির, দিনাজপুর
-
সোনারং জোড়া মন্দির, মুন্সীগঞ্জ
সাধারণ বাংলো ধরনের স্থাপত্য
[সম্পাদনা]
বাংলো স্থাপত্যের সূচনার ঐতিহাসিক ভূমি বাংলা প্রদেশ। [৫] "বাংলো" বলতে আসলে "বাঙ্গালি" বোঝায় এবং বিকৃত অর্থে "বাংলা ধরনের বাড়ি" বোঝায়।[৬] বাড়িগুলো প্রথাগত ভাবেই ছোট ছিল, কেবল একতলা, নিরিবিলি, একটি প্রশস্ত উঠান থাকত, ব্রিটিশরা ব্যবহার করত, গ্রীষ্মে হিমালয় থেকে ফেরার পথে এবং ভারতীয় শহরের বাইরে তারা এগুলো প্রাদেশিক প্রশাসকের বাড়ি হিসেবে ব্যবহার করত। [৭] বাংলো ধরনের বাসাগুলো এখনো গ্রাম বাংলায় বিখ্যাত। আধুনিক কালে মূল স্থাপত্য উপাদান হিসেবে খাঁজকাটা ষ্টীলের পাত ব্যবহার করা হয়। আগে কাঠ, বাঁশ এবং খড় ব্যবহার করা হত। খড় ছাঁদে ব্যবহার করা হত যা ঘরগুলোকে গরমকালেও ঠাণ্ডা রাখত। বাংলোগুলোতে ছাঁদের আবরণ হিসেবে লাল ইট ব্যবহার করা হত।
ইন্দো-সারাসেনিক স্থাপত্যের প্রত্যাবর্তন
[সম্পাদনা]ব্রিটিশ উপনিবেশ যুগে অতীতে প্রচলিত ইন্দো-ইউরোপিয়ান ধরনের উন্নতি হতে থাকে, যা কিনা ভারতীয়, ইউরোপিয়ান এবং মধ্য এশীয় (ইসলামিক) উপাদানের মিশ্রণে তৈরি। উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য হচ্ছে ঢাকার আহসান মঞ্জিল এবং রংপুর শহরে অবস্থিত তাজহাট রাজবাড়ি।
-
শশী বিশ্রামাগার, ময়মনসিংহ
বাংলাদেশের আধুনিক স্থাপত্য
[সম্পাদনা]বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে, স্থাপত্যের উপকরণ, শিল্পকলা এবং প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতির ফলে বাংলাদেশের স্থাপত্য বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্থাপত্যকে এর প্রথাগত রূপ থেকে আধুনিক রূপে নিয়ে এসছে। নগরায়ন এবং আধুনিকায়নের সাথে তাল মিলিয়ে, ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে ব্যাপক মাত্রায় ধারণ করে স্থাপত্য রীতি আধুনিক থেকে আধুনিকতর হচ্ছে।[৮] বাংলাদেশের স্থাপত্য এদেশের মানুষের ইতিহাস এবং জীবন সম্পর্কে গভীর তথ্য প্রকাশ করে।[৯]
ফজলুর রহমান খান ছিলেন একজন অবকাঠামো প্রকৌশলী এবং স্থাপত্যবিদ যিনি আজকের যুগের সুউচ্চ ভবন তৈরির মৌলিক পদ্ধতি গুলোর সূচনা করেন।[১০][১১][১২] "অবকাঠামো প্রকৌশলের আইনস্টাইন" হিসেবে গণ্য[১৩][১৪] খানের "নলাকার নকশা" বহুতল ভবনের নকশায় বিপ্লব নিয়া আসে।[১৫][১৬] ১৯৬০ এর সময় থেকে ৪০-তলার উপরে বেশিরভাগ দালান খানের প্রকৌশল নীতি থেকে প্রাপ্ত একটি নলাকার নকশার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হচ্ছে। উইলিস টাওয়ার যা আমেরিকার দ্বিতীয় উঁচু ভবন (একসময় সর্বোচ্চ ছিল শুধু আমেরিকাতে নয় সারা বিশ্বে এবং অনেক বছর ধরে), জন হ্যানকক সেন্টার, হজ টার্মিনাল প্রভৃতির স্থপতি তিনি। তার নকশা ভবনগুলোকে শুধ শক্তিশালী এবং দক্ষ রূপই দেয় নি, দালান তৈরিতে উপকরণের ব্যবহার ও কমিয়ে আনে (অর্থ সাশ্রয়ী) এবং দালান গুলোর উচ্চতা ক্রমশ বাড়ানো সম্ভব হতে থাকে। নলাকার নকশা, অভ্যন্তরীণ জায়গা বাড়িয়ে তোলে, দালানকে যেকোনো আকার নিতে সাহায্যের মাধ্যমে স্থপতিদের অকল্পনীয় স্বাধীনতা প্রদান করে। [১৭][১৮] তিনি বহুতল ভবনে সহজে উপরে ওঠার জন্য স্কাই লবি আবিষ্কার করেন এবং অবকাঠামো নকশায় কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহার প্রচলন করেন। ফজলুর রহমান ২০ শতকের অগ্রগণ্য অবকাঠামো প্রকৌশলী যিনি এই পেশায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অকল্পনীয় এবং চিরস্থায়ী বদান রেখে গেছেন।[১৩] ২০ শতকের শেষার্ধে আকাশচুম্বী দালান তৈরির মিছিলে অন্য যেকোনো মানুষের চেয়ে ফজলুর রহমানের অবদান অনেক বেশি[১৯] এবং এটর ফলে মানুষের পক্ষে "আকাশের শহরে" বসবাস এবং আকজ করাআ সম্ভব হয়েছে।[২০] খান একটি ধারা প্রবর্তন করেন যা অতুলনীয় এবং স্থাপত্য ও অবকাঠামো প্রকৌশলে দৃষ্টান্ত।[২১][২২]
ছবিঘর
[সম্পাদনা]-
১৭৫২ সালের কান্তজীউ মন্দির
-
বাংলার ১২ ভূইয়ার ঐতিহাসিক রাজধানী, সোনারগাঁও
-
ঢাকার লালবাগ দুর্গ ছিল বাংলায় মোঘল সামরিক শক্তির কেন্দ্রবিন্দু
-
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল
-
পাঁচ তারকা হোটেল- দি ওয়েস্টিন ঢাকা
-
জাতীয় স্মৃতিসৌধ- মহান মুক্তিযুক্তের স্মারক
-
ঢাকার বসুন্ধরা সিটি
-
বাংলাদেশের একমাত্র নভোথিয়েটার (প্ল্যানেটরিয়াম)
-
যমুনা ফিউচার পার্ক - বিশ্বের ১২তম সর্ববৃহৎ শপিং মল
-
সিটি সেন্টার বাংলাদেশ
-
আগারগাওতে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং তৎসংলগ্ন বিসিএস কম্পিউটার সিটি
-
ঢাকায় অবস্থিত বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র
আরও দেখুন
[সম্পাদনা]- বাংলাদেশী স্থপতিদের তালিকা
- মাজহারুল ইসলাম
- হাজী শাহাবাজের মাজার ও মসজিদ
- সোনা মসজিদ
- বাঘা মসজিদ
- খান মোহাম্মদ মৃধা মসজিদ
তথ্যসূত্র
[সম্পাদনা]- ↑ "Visual art and architecture in Bangladesh"। Encyclopædia Britannica। সংগ্রহের তারিখ ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯।
- ↑ মাহবুবুর রহমান (২০১২)। "স্থাপত্যশিল্প"। ইসলাম, সিরাজুল; মিয়া, সাজাহান; খানম, মাহফুজা; আহমেদ, সাব্বীর। বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশের জাতীয় বিশ্বকোষ (২য় সংস্করণ)। ঢাকা, বাংলাদেশ: বাংলাপিডিয়া ট্রাস্ট, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। আইএসবিএন 9843205901। ওএল 30677644M। ওসিএলসি 883871743।
- ↑ The Art of the Pala Empire or Bengal, p.4.
- ↑ "সংরক্ষণাগারভুক্ত অনুলিপি" (পিডিএফ)। ১৫ জুলাই ২০১৫ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৩০ মার্চ ২০১৭।
- ↑ "bungalow"। proz.com।
- ↑ Oxford English Dictionary, "bungalow"; Online Etymology Dictionary
- ↑ "bungalow. The American Heritage Dictionary of the English Language: Fourth Edition. 2000."। bartleby.com। ৮ মার্চ ২০০৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা।
- ↑ উদ্ধৃতি ত্রুটি:
<ref>ট্যাগ বৈধ নয়;banglapediaনামের সূত্রটির জন্য কোন লেখা প্রদান করা হয়নি - ↑ "Appealing Architecture – From Ancient Treasures to Contemporary Landmarks"। Bangladesh.com। ৮ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০০৯।
- ↑ File:Skyscraper structure.png
- ↑ Hong Kong : PHigh-Rise Structural Systems ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ১৭ জুন ২০১২ তারিখে. Darkwing.uoregon.edu. Retrieved on 26 June 2012.
- ↑ "Lehigh University"। lehigh.edu। ১ জুলাই ২০১৯ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৩১ মার্চ ২০১৭।
- ↑ ক খ Richard G. Weingardt, P.E. Structural Engineering Magazine, Tradeshow: Fazlur Rahman Khan ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ৩০ মে ২০১২ তারিখে. Structuremag. February, 2011. Retrieved on 26 June 2012.
- ↑ Zweig, Christina M. (30 March 2011) Structural Engineer ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে. Gostructural.com. Retrieved on 2012-06-26.
- ↑ Richard Weingardt (১০ আগস্ট ২০০৫)। Engineering Legends: Great American Civil Engineers : 32 Profiles of Inspiration and Achievement। ASCE Publications। পৃষ্ঠা 76–। আইএসবিএন 978-0-7844-0801-8। সংগ্রহের তারিখ ২৬ জুন ২০১২।
- ↑ Top 10 world's tallest steel buildings. Constructionweekonline.com. Retrieved on 26 June 2012.
- ↑ On the rise. Constructionweekonline.com (31 January 2011). Retrieved on 2012-06-26.
- ↑ Bayley, Stephen. (5 January 2010) Burj Dubai: The new pinnacle of vanity. Telegraph. Retrieved on 2012-06-26.
- ↑ Richard Weingardt (১০ আগস্ট ২০০৫)। Engineering Legends: Great American Civil Engineers : 32 Profiles of Inspiration and Achievement। ASCE Publications। পৃষ্ঠা 78–। আইএসবিএন 978-0-7844-0801-8। সংগ্রহের তারিখ ২৬ জুন ২০১২।
- ↑ Designing 'cities in the sky' ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ৪ জুন ২০১০ তারিখে. Lehigh University, Engineering & Applied Science. Retrieved on 26 June 2012.
- ↑ Richard Weingardt (১০ আগস্ট ২০০৫)। Engineering Legends: Great American Civil Engineers : 32 Profiles of Inspiration and Achievement। ASCE Publications। পৃষ্ঠা 75–। আইএসবিএন 978-0-7844-0801-8। সংগ্রহের তারিখ ২৬ জুন ২০১২।
- ↑ IALCCE 2012: Keynote Speakers Details ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২৬ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে. Ialcce2012.boku.ac.at. Retrieved on 26 June 2012.




















