হান্স ক্রিশ্চিয়ান ওরস্টেড
হান্স ক্রিশ্চিয়ান ওরস্টেড | |
|---|---|
 | |
| জন্ম | ১৪ আগস্ট ১৭৭৭ রাডকবিং, ডেনমার্ক |
| মৃত্যু | ৯ মার্চ ১৮৫১ (বয়স ৭৩) কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক |
| জাতীয়তা | ড্যানিশ |
| মাতৃশিক্ষায়তন | কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয় (পিএইচডি) (১৭৯৯)[১] |
| পরিচিতির কারণ | তড়িচ্চুম্বকত্বের আবিষ্কার[১] |
| পুরস্কার | কপলি পদক (১৮২০) |
| বৈজ্ঞানিক কর্মজীবন | |
| কর্মক্ষেত্র | পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন |
| প্রতিষ্ঠানসমূহ | কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয় |
| যাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন | ইমানুয়েল কান্ট |
| স্বাক্ষর | |
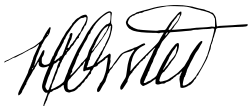 | |
হান্স ক্রিশ্চিয়ান ওরস্টেড (/ˈɜːrstɛd/;[২] ডেনীয়: [ˈhanˀs ˈkʰʁæsd̥jan ˈɶɐ̯sd̥ɛð]; ১৪ অগাস্ট ১৭৭৭ – ৯ মার্চ ১৮৫১) ছিলেন একজন ড্যানিশ পদার্থবিজ্ঞানী এবং রসায়নবিদ। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে, তড়িৎ প্রবাহ চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে, যা ছিল তড়িৎচুম্বকত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তিনি এখনো ওয়েরস্টেডের সূত্র নামে পরিচিত। তিনি মৌলিক পদার্থ অ্যালুমিনিয়াম আবিষ্কার করেন। তিনি উত্তর-কান্টীয় দর্শনের নতুন রুপ দেন এবং ১৯শ শতাব্দীর বিজ্ঞানের আগাম উন্নতি সাধন করেন।[৩] ১৮২৪ সালে তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রচারের জন্য (এসএনইউ) নামে একটি সমাজ গড়ে তোলেন। এছাড়াও তিনি পূর্ববর্তী অনেক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যেগুলো বর্তমানে ড্যানিশ আবহাওয়া ইনস্টিটিউট এবং ডেনিশ পেটেন্ট ও ট্রেডমার্ক অফিসে রপান্তরিত হয়। ওরস্টেড ছিলেন প্রথম আধুনিক চিন্তাবিদ যিনি প্রথম বিশদভাবে চিন্তার পরীক্ষা বর্ণনা করেন এবং নামকরণ করেন।
তিনি ছিলেন তথাকথিত ডেনিশ স্বর্ণযুগের নেতা হান্স ক্রিশ্চিয়ান এন্ডারসেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং রাজনীতিবিদ ও আইনজ্ঞ এন্ডারস স্যান্ডো অরস্টেডের ভাই (যিনি পরবর্তীতে ১৮৫৩–৫৪ সালে ডেনিশ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন)।
সিজিএস পদ্ধতিতে চৌম্বক ক্ষেত্রের একক অরস্টেড (Oe) তার নামানুসারে করা হয়।
প্রথমিক জীবন ও শিক্ষা
[সম্পাদনা]
ওরস্টেড ১৭৭৭ সালে রুডকোবিং শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি বিজ্ঞান নিয়ে আগ্রহী ছিলেন। তিনি তার পিতার সঙ্গে কাজ করতেন, যিনি শহরের একটি ওষুধের দোকানে ফার্মাসিস্ট ছিলেন।[৪] ওরস্টেড এবং তার ভাই অ্যান্ডার্স বাড়িতে তাদের প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন এবং ১৭৯৩ সালে কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে যান, এতে দুইজনই উৎকৃষ্ট ফলাফল অর্জন করেন। ১৭৯৬ সালের মধ্যে ওরস্টেড তার প্রবন্ধের জন্য নন্দনতত্ত্ব এবং পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে সম্মাননা লাভ করেন। ১৭৯৯ সালে তিনি কান্টের কাজের উপর ভিত্তি করে প্রাকৃতিক অধিবিদ্যার স্থাপত্যবিদ্যা শিরোনামে একটি প্রবন্ধের জন্য ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।
১৮০০ সালে আলেসান্দ্রো ভোল্টা তার ভোল্টাইক স্তুপ আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন, যা ওরস্টেডকে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করতে এবং তার প্রথম বৈদ্যুতিক পরীক্ষা করতে অনুপ্রাণিত করে। ১৮০১ সালে ওরস্টেড একটি ভ্রমণ বৃত্তি এবং সরকারি অনুদান পান, যার ফলে তিনি ইউরোপজুড়ে তিন বছর ভ্রমণ করেন। তিনি বার্লিন এবং প্যারিসসহ ইউরোপের বিভিন্ন বিজ্ঞান কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।[৫]
জার্মানিতে ওরস্টেড জোহান উইলহেম রিটার নামক এক পদার্থবিজ্ঞানীর সাথে সাক্ষাৎ করেন, যিনি বিশ্বাস করতেন যে বৈদ্যুতিক শক্তি এবং চুম্বকত্বের মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। এই ধারণাটি ওরস্টেডের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল, কারণ তিনি কান্তের দার্শনিক চিন্তাভাবনার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, যা প্রাকৃতিক জগতের ঐক্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে।[৪][৬][পৃষ্ঠা নম্বর প্রয়োজন] ওরস্টেড এবং রিটার-এর আলোচনা তাকে পদার্থবিজ্ঞান অধ্যয়নে আগ্রহী করে তোলে। ১৮০৬ সালে তিনি কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়-এ অধ্যাপক পদে নিয়োগ পান এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহ এবং শব্দতত্ত্বের উপর গবেষণা চালাতে থাকেন। তার নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন প্রোগ্রাম গঠন করা হয় এবং নতুন ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠিত হয়। [তথ্যসূত্র প্রয়োজন]
ওরস্টেড ১৮০৬ সালের শরৎকালে উইলিয়াম ক্রিস্টোফার জেইস-কে তার পরিবারের বাড়িতে স্বাগত জানান। তিনি জেইস-কে তার লেকচারিং সহকারী পদ প্রদান করেন এবং তরুণ রসায়নবিদকে নিজের তত্ত্বাবধানে নেন। ১৮১২ সালে ওরস্টেড আবার জার্মানি এবং ফ্রান্স সফর করেন, যখন তিনি Videnskaben om Naturens Almindelige Love এবং Første Indledning til den Almindelige Naturlære (১৮১১) গ্রন্থ দুটি প্রকাশ করেন।
ওরস্টেড আধুনিক চিন্তাবিদদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি স্পষ্টভাবে চিন্তা পরীক্ষা বর্ণনা এবং নামকরণ করেন। তিনি প্রায় ১৮১২ সালে লাতিন-জার্মান শব্দ গেডেনকেন এক্সপেরিমেন্ট এবং ১৮২০ সালে জার্মান শব্দ গেডানকেনভারসুচ ব্যবহার করেন।[৭]
১৮১৯ সালে ওরস্টেড গোলমরিচের গাছ থেকে প্রথম পাইপারিন নিষ্কাশন করেন এবং এর নামকরণ করেন, যা ছিল সাদা ও কালো গোলমরিচের উৎস।[৮]
ওরস্টেড ১৮২২ সালে একটি নতুন ধরনের পিজোমিটারের নকশা করেন, যা তরলের সংকোচনক্ষমতা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়।[৯]
তাড়িৎচৌম্বকত্ব
[সম্পাদনা]১৮২০ সালে ওরস্টেড তার একটি আবিষ্কার প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি দেখান যে একটি কম্পাসের কাটা একটি নিকটস্থ বৈদ্যুতিক প্রবাহ দ্বারা চুম্বক উত্তর থেকে বিচ্যুত হয়, যা তড়িৎ এবং চুম্বকত্বের মধ্যে সরাসরি সম্পর্কের প্রমাণ প্রদান করে।[১০] ওরস্টেড যে এটি একটি বক্তৃতার সময় একভাবে খুঁজে পেয়েছিলেন, এমন প্রচলিত গল্পটি একটি মিথ। তিনি আসলে ১৮১৮ সাল থেকেই বৈদ্যুতিকতা এবং চুম্বকত্বের মধ্যে একটি সংযোগ খুঁজছিলেন, কিন্তু যে ফলাফলগুলো তিনি পাচ্ছিলেন, তা তাকে বেশ বিভ্রান্ত করেছিল।[১১][১০]:২৭৩
তার প্রাথমিক ব্যাখ্যা ছিল যে একটি বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালিত তার থেকে চুম্বকীয় প্রভাব সব দিক থেকে বিচ্ছুরিত হয়, যেমন আলো এবং তাপ বিচ্ছুরিত হয়। তিন মাস পর, তিনি আরও গভীর গবেষণা শুরু করেন এবং কিছুদিন পরেই তিনি তার আবিষ্কার প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি দেখান যে একটি বৈদ্যুতিক প্রবাহ তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলে একটি বৃত্তাকার চুম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি হয়। তার এই আবিষ্কারের জন্য, রয়েল সোসাইটি অফ লন্ডন ওরস্টেড-কে ১৮২০ সালে কোপলি মেডেল পুরস্কৃত করে এবং ফরাসি একাডেমি তাকে ৩,০০০ ফরাসি ফ্রাঙ্ক প্রদান করে।
ওরস্টেড-এর আবিষ্কার বৈদ্যুতিন গতিবিদ্যা (ইলেকট্রোডাইনামিক্স) বিষয়ে অনেক গবেষণার সূচনা করে, যা ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী অ্যান্ড্রে-মারি অ্যাম্পেয়ার-এর কাজকে প্রভাবিত করে, যিনি বৈদ্যুতিক প্রবাহ বহনকারী পরিবাহকদের মধ্যে চুম্বকীয় শক্তির প্রতিনিধিত্ব করতে একটি একক গাণিতিক সূত্র তৈরি করেন। ওরস্টেড-এর কাজ আরও একটি বড় পদক্ষেপ ছিল শক্তির একটি একত্রীত ধারণার দিকে।
ওরস্টেড-এর প্রভাবের ফলে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ তৈরিতে বিপ্লব ঘটে। এমন একটি টেলিগ্রাফের সম্ভাবনা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গণিতজ্ঞ পিয়ের-সিমন লাপ্লাস দ্বারা প্রস্তাবিত হয় এবং অ্যাম্পেয়ার ওরস্টেড-এর আবিষ্কারের একই বছর লাপ্লাসের ধারণার ভিত্তিতে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।[১০]:৩০২–৩০৩ তবে, এটি বাণিজ্যিকভাবে বাস্তবতা হয়ে উঠতে প্রায় দুই দশক সময় নেয়।
পরবর্তী বছরগুলো
[সম্পাদনা]
ওরস্টেড ১৮২১ সালের মার্চ মাসে রয়েল সোসাইটি অফ এডিনবার্গের ফেলো নির্বাচিত হন,[১২] ১৮২১ সালের এপ্রিল মাসে রয়েল সোসাইটি অফ লন্ডনের ফরেন মেম্বার নির্বাচিত হন,১৮২২ সালে রয়েল সুইডিশ একাডেমি অফ সায়েন্সেস-এর ফরেন মেম্বার হন, ১৮২৯ সালে আমেরিকান ফিলোসফিক্যাল সোসাইটি-এর সদস্য হন,[১৩] এবং ১৮৪৯ সালে আমেরিকান একাডেমি অফ আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস-এর ফরেন অনারারি মেম্বার হন।[১৪]
তিনি ১৮২৪ সালে (ন্যাচারাল সায়েন্সের বিস্তার সংস্থা, এসএনইউ) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এছাড়াও পূর্ববর্তী সংগঠনগুলোর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, যা পরে ড্যানিশ মেটিওরোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট এবং ড্যানিশ পেটেন্ট এবং ট্রেডমার্ক অফিস হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৮২৯ সালে ওরস্টেড (কলেজ অফ অ্যাডভান্সড টেকনোলজি) প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীতে টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অফ ডেনমার্ক (ডিটিইউ) নামে পুনঃনামকরণ করা হয়।[১৫]
১৮২৪ সালে ওরস্টেড রসায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন, কারণ তিনি প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি সফলভাবে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু আকারে উৎপাদন করেন, যদিও এটি কম বিশুদ্ধ অবস্থায় ছিল।[১৬][১৭] ১৮০৮ সালে হাম্প্রি ডেভি ধাতুটির অস্তিত্বের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন, যার নাম তিনি রেখেছিলেন অ্যালুমিনিয়াম। তবে তিনি বৈদ্যুতোলাইসিস প্রক্রিয়া ব্যবহার করে এটি পৃথক করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা সফল হয়নি; তার সবচেয়ে কাছাকাছি ফল ছিল অ্যালুমিনিয়াম-আয়রন অ্যালয়।[১৮] ওরস্টেড অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডকে পটাসিয়াম এমালগাম (পটাসিয়াম এবং পারদ এর একটি মিশ্রণ) সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে ধাতুর বিশুদ্ধ রূপ পৃথক করতে সফল হন এবং তারপর পারদ বাষ্পীভূত করে তার থেকে ছোট "টুকরো" ধাতু বের করেন, যা তিনি টিনের মতো দেখতে বলেছিলেন।[১৬][টীকা ১] তিনি ১৮২৫ সালের শুরুতে ড্যানিশ একাডেমি অফ সায়েন্সেস-এর সভায় তার ফলাফল এবং ধাতুর একটি নমুনা উপস্থাপন করেন, কিন্তু মনে হয় তিনি তার আবিষ্কারটি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ভাবেননি।[১৯] এই দ্বিধা, এবং ড্যানিশ একাডেমির জার্নালের সীমিত পাঠকগণের কারণে যেখানে ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল, তাৎক্ষণিকভাবে বিজ্ঞানী সমাজের নজর এড়িয়ে যায়।[১৯][২০] অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে, ১৮২৭ সালে ওরস্টেড তার বন্ধু, জার্মান রসায়নবিদ ফ্রিডরিখ ওয়েহলার-কে গবেষণাটি চালানোর অনুমতি দেন।[১৯] ওয়েহলার তার নিজের ডিজাইন করা প্রক্রিয়া ব্যবহার করে কিছুদিন পরেই প্রায় ৩০ গ্রাম (১.১ আউন্স) অ্যালুমিনিয়াম পাউডার উৎপাদন করতে সক্ষম হন, এবং শেষমেশ ১৮৪৫ সালে তিনি এমন পরিমাণে কঠিন ধাতু পৃথক করেন যা তার শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করার জন্য যথেষ্ট ছিল।[১৭]

ওরস্টেড ১৮৫১ সালে কোপেনহেগেনে মৃত্যুবরণ করেন, তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর, এবং তাকে অ্যাসিস্টেন্স সেমেট্রিতে দাফন করা হয়।
ঐতিহ্য
[সম্পাদনা]
সেন্টিমিটার-গ্রাম-সেকেন্ড সিস্টেম (সিজিএস) ম্যাগনেটিক ইনডাকশন (অর্শটেড) এককের নামকরণ করা হয়েছে তার বৈদ্যুতিন চুম্বকত্বের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য।
ডেনিশ অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস (ডিওএনজি) কোম্পানিটি তার জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে পরিবর্তিত হয়ে ওরস্টেড নামে পুনর্নামকরণ করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে কোম্পানিটি বিশ্বজুড়ে অন্যতম প্রধান অফশোর উইন্ডফার্ম ডেভেলপার ও অপারেটর হয়ে ওঠার সংকেত দেয়।
প্রথম ডেনিশ স্যাটেলাইট, যা ১৯৯৯ সালে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল, সেটিও ওরস্টেড এর নামে নামকরণ করা হয়েছে।
স্থানীয় নামকরণ
[সম্পাদনা]কোপেনহেগেনের ওরস্টেড ১৮৭৯ সালে ওরস্টেড এবং তার ভাইয়ের নামে নামকরণ করা হয়। এবং গালটেন-এ রাস্তা তার নামে নামকরণ করা হয়েছে।
কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের এবং গণিতবিদ্যা বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এর ভবনগুলো এইচ.সি ওর্স্টেড ইনস্টিটিউট নামে পরিচিত, যা তার নামে নামকরণ করা হয়েছে। এইচ.সি ওয়েস্টাড নামের একটি ছাত্রাবাসও রয়েছে।
ভাস্কর্য এবং স্মৃতিস্তম্ভ
[সম্পাদনা]
১৮৮০ সালে ওরস্টেড পার্কে একটি ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়। তার বাসস্থান ও কর্মস্থলে অধ্যয়নরত ভবনের গেটে একটি স্মৃতিফলক স্থাপন করা হয়েছে।
১৮৮৫ সালে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রাকৃতিক ইতিহাস যাদুঘরে ওরস্টেড এর একটি ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়।
ওরস্টেড এর প্রতিচ্ছবি ডেনিশ মুদ্রায় দুইবার উপস্থিত হয়েছে; প্রথমবার ১৮৭৫ সালে ৫০০ ক্রোনার নোটে, এবং দ্বিতীয়বার ১৯৬২ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত ১০০ ক্রোনার নোটে।[২১]
পুরস্কার এবং বক্তৃতা
[সম্পাদনা]ওরস্টেড এর নামে দুটি মেডেল পুরস্কৃত হয়: এইচ. সি. ওরস্টেড পদক ডেনিশ বিজ্ঞানীদের জন্য, যা ডেনিশ সোসাইটি ফর দ্য ডিসেমিনেশন অফ ন্যাচারাল সায়েন্স (এসএনইউ) দ্বারা পুরস্কৃত হয়, যা ওরস্টেড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং ওরস্টেড পদক আমেরিকায় পদার্থবিদ্যার শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য, যা আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিক্স টিচার্স দ্বারা পুরস্কৃত হয়।
ডেনমার্কের টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি হোস্ট করে এইচ. সি. ওরস্টেড বক্তৃতা সিরিজ, যা বিশ্বের খ্যাতনামা গবেষকদের জন্য।[২২]
কাজসমূহ
[সম্পাদনা]ওরস্টেড ছিলেন একজন প্রকাশিত কবি এবং বিজ্ঞানী। তার কবিতার সংকলন ("দ্য এয়ারশিপ") ছিল তার সহকর্মী পদার্থবিদ এবং মঞ্চ জাদুকর ইতিয়েন-গ্যাসপার্ড রবার্ট এর বেলুন ভ্রমণের দ্বারা অনুপ্রাণিত।[২৩]
- Ørsted, H. C. (১৮৩৬)। Luftskibet, et Digt [The Airship, a Poem] (ডেনীয় ভাষায়)। København: Gyldendal। ওসিএলসি 28930872।
১৮৫০ সালে, মৃত্যুর পূর্বে, তিনি জার্মানিতে দুটি খণ্ডের একটি দার্শনিক প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশের জন্য জমা দেন, যার শিরোনাম ছিল Der Geist in der Natur ("প্রকৃতির আত্মা")। এটি ইংরেজিতে অনূদিত হয় এবং ১৮৫২ সালে এক খণ্ডে প্রকাশিত হয়, তার মৃত্যুর এক বছর পর।
- Ørsted, H. C. (১৮৫০–১৮৫১)। Der Geist in der Natur [The Soul in Nature] (জার্মান ভাষায়)। München: J. G. Cotta। ওসিএলসি 653954।
- —— (১৮৫২)। The Soul in Nature, with Supplementary Contributions। Bohn's scientific library [16]। Horner, L.; Horner, J. B. কর্তৃক অনূদিত। London: Henry G. Bohn। hdl:2027/loc.ark:/13960/t4zg7w20q
 । ওসিএলসি 8719272।
। ওসিএলসি 8719272।
- —— (১৮৫২)। The Soul in Nature, with Supplementary Contributions। Bohn's scientific library [16]। Horner, L.; Horner, J. B. কর্তৃক অনূদিত। London: Henry G. Bohn। hdl:2027/loc.ark:/13960/t4zg7w20q
অন্যান্য কাজ:
- Ørsted, H. C. (১৮০৭)। "Betragtninger over Chemiens Historie" [Considerations on the History of Chemistry]। Det Skandinaviske Litteraturselskabs Skrifter (ডেনীয় ভাষায়)। København: Andreas Seidelin। 2: 1–54। ওসিএলসি 872505637।
- —— (১৮০৯)। Videnskaben om Naturens almindelige Love [The Science of the General Laws of Nature] (ডেনীয় ভাষায়)। København: Fr. Brummer। ওসিএলসি 488860438।
- —— (১৮১২)। Ansicht der chemischen Naturgesetze, durch die neuern Entdeckungen gewonnen [View of the Chemical Laws of Nature Gained Through Recent Discoveries] (জার্মান ভাষায়)। Berlin: Realschulbuchhandlung। ওসিএলসি 28640794।
- —— (১৮১৪)। Imod den store Anklager [Against the Great Accuser] (ডেনীয় ভাষায়)। København: Andreas Seidelin। ওসিএলসি 19092207।
- —— (১৮২০)। "Experiments on the Effect of a Current of Electricity on the Magnetic Needle"। Thomson, T.। Annals of Philosophy; or, Magazine of Chemistry, Mineralogy, Mechanics, Natural History, Agriculture, and the Arts। XVI। London: Baldwin, Cradock, and Joy। পৃষ্ঠা 273–276। hdl:2027/osu.32435051156651
 । ওসিএলসি 9529852।
। ওসিএলসি 9529852। - —— (১৮৪৪)। Naturlærens mechaniske Deel [The Mechanical Part of Natural Learning] (ডেনীয় ভাষায়)। København: C. A. Reitzel। hdl:2027/njp.32101058433184
 । ওসিএলসি 22224906।
। ওসিএলসি 22224906। - —— (১৮৫১)। Der mechanische Theil der Naturlehre [The Mechanical Part of Natural Learning] (জার্মান ভাষায়)। Braunschweig: Friedrich Vieweg und Sohn। ওএল 6960604M
 । ওসিএলসি 9489733।
। ওসিএলসি 9489733। - Harding, M. C., সম্পাদক (১৯২০)। Correspondance de H. C. Örsted avec divers savants [The Correspondence of H. C. Örsted with Various Scholars]। Copenhaugue: H. Aschehoug & Co.। ওসিএলসি 11070734।
- Volume I, containing correspondence with Jöns Jacob Berzelius, Christopher Hansteen, and Christian Samuel Weiss.
- Volume II, containing correspondence with Johann Wilhelm Ritter and numerous others, including Michael Faraday and Carl Friedrich Gauss.
Ørsted এর অনেক গবেষণা প্রবন্ধ প্রথমবার ইংরেজিতে উপলব্ধ করা হয়েছিল একটি সংকলনে, যা ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয়:[২৪]
- Ørsted, H. C. (১৯৯৮)। Jelved, K.; Jackson, A. D.; Knudsen, O., সম্পাদকগণ। Selected Scientific Works of Hans Christian Ørsted। Princeton University Press। আইএসবিএন 978-0-69104-334-0। ওসিএলসি 36393437। জেস্টোর j.ctt7zvhx2।
তথ্যসূত্র
[সম্পাদনা]- ↑ ক খ http://www.rare-earth-magnets.com/t-hans-christian-oersted.aspx
- ↑ "Oersted". Random House Webster's Unabridged Dictionary.
- ↑ Brian, R.M. & Cohen, R.S. (2007). Hans Christian Ørsted and the Romantic Legacy in Science, Boston Studies in the Philosophy of Science, Vol. 241.
- ↑ ক খ Jacobsen, A. S.; Knudsen, O. (১৪ এপ্রিল ২০২১)। "H.C. Ørsted"। Den Store Danske (ডেনীয় ভাষায়)। Gyldendal। সংগ্রহের তারিখ ১২ এপ্রিল ২০২৩।
- ↑ "Inspiration fra Europa – planer i København" [Inspiration from Europe – Plans in Copenhagen] (ডেনীয় ভাষায়)। Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩। সংগ্রহের তারিখ ১২ এপ্রিল ২০২৩।
- ↑ Brain, R. M.; Cohen, R. S.; Knudsen, O., সম্পাদকগণ (২০০৭)। Hans Christian Ørsted and the Romantic Legacy in Science: Ideas, Disciplines, Practices। Boston Studies in the Philosophy and History of Science। 241। Dordrecht: Springer। আইএসবিএন 978-1-40202-979-0। ওসিএলসি 181067920। ডিওআই:10.1007/978-1-4020-2987-5।
- ↑ Witt-Hansen, J. (১৯৭৬)। "H.C. Ørsted, Immanuel Kant, and the Thought Experiment"। Danish Yearbook of Philosophy। 13 (1): 48–65। আইএসএসএন 0070-2749। ডিওআই:10.1163/24689300-01301004।
- ↑ Ørsted, Hans Christian (১৮২০)। "Über das Piperin, ein neues Pflanzenalkaloid" [On piperine, a new plant alkaloid]। Schweiggers Journal für Chemie und Physik (জার্মান ভাষায়)। 29 (1): 80–82।
- ↑ Aitken, F.; Foulc, J.-N. (২০১৯)। From Tait's Work on the Compressibility of Seawater to Equations-of-State for Liquids। From Deep Sea to Laboratory। 3। London: ISTE। আইএসবিএন 978-1-78630-376-9। এসটুসিআইডি 204258765। ডিওআই:10.1002/9781119663362।
- ↑ ক খ গ Fahie, J. J. (১৮৮৪)। A History of Electric Telegraphy to the Year 1837। London: E. & F. N. Spon। ওএল 6993294M
 । ওসিএলসি 1417165।
। ওসিএলসি 1417165।
- ↑ Martins, R. A. (২০০৩)। "Resistance to the Discovery of Electromagnetism: Ørsted and the Symmetry of the Magnetic Field" (পিডিএফ)। Bevilacqua, F.; Giannetto, E.। Volta and the History of Electricity। Milano: Editore Ulrico Hoepli। পৃষ্ঠা 245–265। আইএসবিএন 978-8-82033-284-6। ওসিএলসি 1261807533। ২৩ জুলাই ২০১১ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা।
- ↑ Waterston, C. D.; Macmillan Shearer, A. (জুলাই ২০০৬)। Biographical Index of the Former Fellows of the Royal Society of Edinburgh, 1783–2002 (পিডিএফ)। II। The Royal Society of Edinburgh। পৃষ্ঠা 703 (in work p. 215)। আইএসবিএন 978-0-90219-884-5। সংগ্রহের তারিখ ২০ মার্চ ২০২৩।
- ↑ "APS Member History"। American Philosophical Society। সংগ্রহের তারিখ ৭ এপ্রিল ২০২১।
- ↑ "Chapter O" (পিডিএফ)। Members of the American Academy of Arts & Sciences: 1780–2012। American Academy of Arts and Sciences। পৃষ্ঠা 401। ২০ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬।
- ↑ "History of DTU"। Kongens Lyngby: Danmarks Tekniske Universitet। ২০০৯-০৯-০২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০০৯-০৮-১৪।
- ↑ ক খ Ørsted, H. C., সম্পাদক (১৮২৫)। "Physisk Classe"। Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider fra 31 Mai 1824 til 31 Mai 1825 (ডেনীয় ভাষায়)। København। পৃষ্ঠা 15–16। hdl:2027/osu.32435054254693
 । আইএসএসএন 0369-7169। ওসিএলসি 32565767।
। আইএসএসএন 0369-7169। ওসিএলসি 32565767।
- ↑ ক খ গ Drozdov, A. (২০০৭)। Aluminium: The Thirteenth Element (পিডিএফ)। Moscow: RUSAL Library। পৃষ্ঠা 36–37। আইএসবিএন 978-5-91523-002-5। ১৬ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০ মার্চ ২০২৩।
- ↑ Kvande, H. (২০০৮)। "Two hundred years of aluminum... or is it aluminium?"। JOM। 60 (8): 23–24। এসটুসিআইডি 135517326। ডিওআই:10.1007/s11837-008-0102-3। বিবকোড:2008JOM....60h..23K।
- ↑ ক খ গ Christensen, D. C. (২০১৩)। "Aluminium: Priority and Nationalism"। Hans Christian Ørsted: Reading Nature's Mind। Oxford University Press। পৃষ্ঠা 424–430। আইএসবিএন 978-0-19966-926-4। ওসিএলসি 847943710। ডিওআই:10.1093/acprof:oso/9780199669264.001.0001।
- ↑ Fontani, M.; Costa, M.; Orna, M. V. (২০১৫)। The Lost Elements: The Periodic Table's Shadow Side। Oxford University Press। পৃষ্ঠা 30। আইএসবিএন 978-0-19938-334-4। ওসিএলসি 873238266।
- ↑ "Sedler og Mønter: Portræt- og Landskabsserien" [Notes and Coins: The Portrait and Landscape Series] (ডেনীয় ভাষায়)। København: Danmarks Nationalbank। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪। সংগ্রহের তারিখ ২০ মার্চ ২০২৩।
- ↑ "DTU Ørsted Lectures"। Kongens Lyngby: Danmarks Tekniske Universitet। সংগ্রহের তারিখ ২০ মার্চ ২০২৩।
- ↑ "1802: Balloon Expedition over Copenhagen"। The Soul in Nature: The Danish Golden Age 1800–1850। København: Nationalmuseet। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৩০ জুলাই ২০০৭।
- ↑ Caneva, K. L. (১৯৯৯)। "Book Review: Hans Christian Ørsted, 'Selected Scientific Works of Hans Christian Ørsted', Edited and translated by Karen Jelved, Andrew D. Jackson, and Ole Knudsen ..."। Isis। 90 (4): 819–820। ডিওআই:10.1086/384554।
আরও পড়ুন
[সম্পাদনা]
- Brain, R. M.; ও অন্যান্য (২০০৭)। Hans Christian Ørsted and the Romantic Legacy in Science. Ideas, Disciplines, Practices। Boston Studies in the Philosophy of Science, 241। Dordrecht। পৃষ্ঠা 273–338।
- Christensen, D. C. (২০১৩)। Hans Christian Ørsted। Oxford: Oxford University Press। আইএসবিএন 978-0-19-966926-4।
- Dibner, Bern, Oersted and the discovery of electromagnetism, New York, Blaisdell (1962).
- Ole Immanuel Franksen, H. C. Ørsted – a man of the two cultures, Strandbergs Forlag, Birkerød, Denmark (1981). (Note: Both the original Latin version and the English translation of his 1820 paper "Experiments on the effect of a current of electricity on the magnetic needle" can be found in this book.)
বহিঃসংযোগ
[সম্পাদনা] উইকিমিডিয়া কমন্সে হান্স ক্রিশ্চিয়ান ওরস্টেড সম্পর্কিত মিডিয়া দেখুন।
উইকিমিডিয়া কমন্সে হান্স ক্রিশ্চিয়ান ওরস্টেড সম্পর্কিত মিডিয়া দেখুন।- Physics Tree: হান্স ক্রিশ্চিয়ান ওরস্টেড
- Interactive Java Tutorial on Oersted's Compass Experiment National High Magnetic Field Laboratory
- The soul in nature : with supplementary contributions, London: H. G. Bohn, 1852.
- ফাইন্ড এ গ্রেইভে হান্স ক্রিশ্চিয়ান ওরস্টেড (ইংরেজি)
 "Oersted, Hans Christian"। এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা। ১৯২০।
"Oersted, Hans Christian"। এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা। ১৯২০।
টেমপ্লেট:Copley Medallists 1801-1850 টেমপ্লেট:Danish Golden Age
উদ্ধৃতি ত্রুটি: "টীকা" নামক গ্রুপের জন্য <ref> ট্যাগ রয়েছে, কিন্তু এর জন্য কোন সঙ্গতিপূর্ণ <references group="টীকা"/> ট্যাগ পাওয়া যায়নি